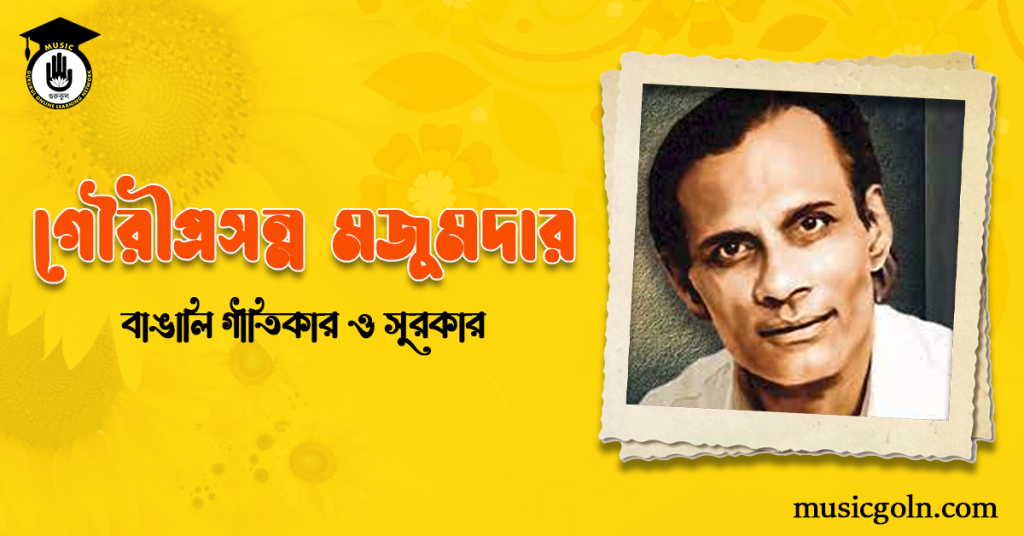গৌরীপ্রসন্ন মজুমদার বাংলা আধুনিক ও চলচ্চিত্র সংগীতের বিশিষ্ট গীতিকার ও সুরকার। বিংশ শতাব্দীর দ্বিতীয়ার্ধ জুড়ে বাংলা ছায়াছবি ও আধুনিক গানের জগতকে যাঁরা প্রেমাবেগ-উষ্ণ রেখেছিলেন তিনি তাঁদের একজন। গীত রচনায় তার বৈশিষ্ট্য শব্দচয়নে। মান্না দের গাওয়া তার লেখা ‘কফি হাউসের সেই আড্ডাটা আজ আর নেই’ ২০০৪ সালে বিবিসির জরিপে সর্বকালের সর্বশ্রেষ্ঠ ২০টি বাংলা গানে ঠাঁই পেয়েছে। গৌরীপ্রসন্নের জন্ম ৫ ডিসেম্বর ১৯২৪।
গৌরীপ্রসন্ন মজুমদারের বিখ্যাত কিছু গান:
- অলির কথা শুনে বকুল হাসে
- আমার গানের স্বরলিপি
- আমার স্বপ্নে দেখা রাজকন্যা
- আমি যামিনী তুমি শশী হে
- এই পথ যদি না শেষ হয়
- এই মেঘলা দিনে একলা ঘরে থাকে না তো মন
- এই মোম জোছনায় অঙ্গ ভিজিয়ে
- এই সুন্দর স্বর্ণালি সন্ধ্যায়, এ কী বন্ধনে জড়ালে গো বন্ধু
- এমন দিন আসতে পারে
- ও নদীরে একটি কথা শুধাই শুধু তোমারে
- ও মালিক সারাজীবন কাঁদালে
- কফি হাউসের সেই আড্ডাটা আজ আর নেই
- কী আশায় বাঁধি খেলাঘর
- কেন দূরে থাকো শুধু আড়াল রাখো কে তুমি কে তুমি আমায় ডাকো
- গানে মোর ইন্দ্রধনু
- তুমি না হয় রহিতে কাছে
- তোমার সমাধি ফুলে ফুলে ঢাকা
- নীর ছোট আকাশ তো বড়
- পথের ক্লান্তি ভুলে
- প্রেম একবার এসেছিল নীরবে
- বাঁশি শুনে আর কাজ নাই সে যে ডাকাতিয়া বাঁশি
- মাগো, ভাবনা কেন, আমরা তোমার শান্তিপ্রিয় শান্ত ছেলে
- শোন একটি মুজিবরের থেকে লক্ষ মুজিবরের কন্ঠস্বরের ধ্বনি প্রতিধ্বনি আকাশে বাতাসে ওঠে রণি… বাংলাদেশ, আমার বাংলাদেশ
সৌমিত জয়দ্বীপ “গৌরীপ্রসন্ন মজুমদার: দ্য আনসাং হিরো!” শিরনামে তার লেখায় লিখেছেন:
তাকে বলা যেতে পারে বাংলা সঙ্গীত ইতিহাসের ‘আনসাং হিরো’। আহা, কত কত কালজয়ী গান তার কলমের কালিতে লেখা হয়েছে, অথচ তিনি রয়ে গেছেন একদম অন্তরালে! তিনি ‘অদ্বিতীয়’ গৌরীপ্রসন্ন মজুমদার (৫ ডিসেম্বর ১৯২৫-২০ অগাস্ট ১৯৮৬)।
সঙ্গীত শিল্পের (এমনকি চলচ্চিত্রেরও) এই শ্রেষ্ঠত্ববাদী ও কৃর্তত্ববাদী ‘ডগমা’টা ভাঙা দরকার। গাইতে মেধা লাগে নিশ্চয়ই। তবে কি গান সুর করতে বা গীতি লিখতে মেধা লাগে না? তাহলে, আকাশে-বাতাসে কেন শুধুই সঙ্গীতশিল্পীর জয়ধ্বনি, রাজত্ব?
মানুষ আজকে স্যোশাল মিডিয়ার দাস হয়েছে বটে। কিন্তু, এই রাজত্বের প্রশ্নটা শেষ পর্যন্ত ডিল করে গণমাধ্যম। গণমাধ্যম কি তবে পক্ষপাতদুষ্ট? আমি বলব– না। মেনে নিতে হবে যে, গণমাধ্যম প্রচলিত হওয়ার বহু আগে থেকেই, মানুষ নিজেই একটা মিডিয়া হিসেবে এবং খুবই বায়াসড মিডিয়া হিসেবে আবির্ভূত হয়েছে।
এটা খুব ভালো বোঝা যায় সঙ্গীত ও চলচ্চিত্রে। যত পাদপ্রদীপের আলো, সব সামনের জনের। পেছনে যিনি বা যারা পুরো কাঠামোটা দাঁড় করিয়ে দিলেন, বহু কষ্টে তার বা তাদের নাম মস্তিষ্কে ঢুকিয়ে নিতেও কষ্ট হয় মানুষের।
এমনকি ঘটনা এতটাই গভীরে যে, চলচ্চিত্রে প্লেব্যাক সিঙ্গারও পর্যন্ত নায়ক-নায়িকার ঔজ্জ্বল্যের কাছে আর লাইমলাইট পান না। সেখানে গীতিকার-সুরকার তো আলোকবর্ষ দূরের ব্যাপার! মানুষ নিজেই যেহেতু খুবই শক্তিশালী মিডিয়া, ফলে দর্শকের মনন দিয়ে সে যা দেখে তাকেই সত্য মানে। সত্যের পেছনে যা, তা তাকে চিন্তা করতে হবে কেন!
আমার মনে হয়, গৌরীপ্রসন্ন মজুমদার মানুষের এই ‘গুণ’টির করুণ শিকারে পরিণত হয়েছেন! ফলে, বাঙালি সমাজে খুব বেশি ‘রা’ নেই তাকে ঘিরে। অথচ, তিনি ‘কফি হাউজের সেই আড্ডাটা আজ আর নেই’ না লিখলে মান্না দে কোথা থেকে গাইতেন এমন অমর ও কালজয়ী গান!
২.
গৌরী প্রসন্ন মজুমদারের গান দেখেই বুঝে নেয়া যেতে পারে, তিনি কী দুর্দান্ত গীতিকারই না ছিলেন। তবে, শুধু ‘গীতিকার’ বললে তার প্রতি ভীষণ অবিচার করা হবে।
ভালোবেসে কেউ কেউ তাকে হয়তো ‘গীতিকবি’ও বলতে পারে। কিন্তু, আমার ক্ষুদ্র বোধবুদ্ধিতে তিনি আসলে বড় কবি হওয়ার মনন নিয়েই জন্মেছিলেন। সেটা এতটাই যে, শিক্ষাজীবনেই কালিদাসের ‘মেঘদূতম’ ইংরেজিতে অনুবাদ করে ফেলেছিলেন তিনি! কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে ইংরেজি ও বাংলা উভয় সাহিত্যে স্নাতকোত্তর যার, তার কাব্য প্রতিভার উন্মেষ ঘটেছিল এভাবেই। কিন্তু, ঘটনাচক্রে আমরা তাকে ‘প্রিয় গীতিকার’ বলয়ের বাইরে ভাবতে পারিনি।
আমার কাছে অবশ্য তিনি আপাদমস্তক এক কবি। বড় কবি, যিনি জীবনের মোড় বদলে হয়ে উঠেছিলেন একজন বড় মাপের সঙ্গীতসাধক। ফলে, তার কীর্তি ও কৃতি ওই গীতিকার হিসেবেই আমাদের মেপে নিতে হয় বারংবার। তবে, আশা করা যায়, একদিন হয়তো তার কাব্যপ্রতিভা বিষয়ে সাহিত্য বিভাগগুলোতে গবেষণার উদ্যোগ নেওয়া হবে। যদিও আমাদের সাহিত্য বিভাগগুলোতে শিল্প হিসেবে সঙ্গীতধারাটি খুবই ব্রাত্য, তবুও কোথাও কোথাও লালন-হাসন যখন একবার ঢুকতে পেরেছেন, তখন তাদের উত্তরসাধকরাও পারবেন।
বাংলাদেশে এ নিয়ে তর্কটা বহু দিনের। তবে, সেটা আরও জোরাল হয়ে ওঠে ২০১৬ সালের পর। সে বছর নিজের লেখা গীতিকাব্যের জন্য সাহিত্যে নোবেল পুরস্কার পান বিখ্যাত মার্কিন গণসঙ্গীত শিল্পী ও বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধের অকৃত্রিম বন্ধু বব ডিলান। ডিলান বরাবরই মনে করেন, ‘আই কনসিডার মাইসেলফ অ্যা পোয়েট ফার্স্ট অ্যান্ড অ্যা মিউজিসিয়ান সেকেন্ড। আই লিভ লাইক অ্যা পোয়েট অ্যান্ড আই উইল ডাই লাইক অ্যা পোয়েট।’
এই তর্কে ডিলানের সায় আছে বোঝা যাচ্ছে। তবে, যুক্তিবুদ্ধির বদৌলতে সাহিত্যের একজন শিক্ষার্থী হিসেবে আমি সঙ্গীতকে সাহিত্যের অংশ ও অঙ্গ মনে করি; প্রতিষ্ঠান মনে না করলে সেটা তার সংকীর্ণতা এবং একই সঙ্গে তার নিজস্ব বোঝাপড়ার সমস্যা।
ডিলান মার্কিন দেশের লোক। গৌরীপ্রসন্ন মজুমদার আমাদের পাবনার মানুষ। কিন্তু, তাদের চিন্তায় ফারাক খুব বেশি দেখি না কবিতা ও গীতিকবিতা প্রসঙ্গে। ১৯৮৬ সালের ২০ অগাস্ট, অর্থাৎ আজ থেকে ৩৪ বছর আগে, দীর্ঘ ১০ বছর ক্যান্সারে ভুগে তিনি মারা যান। ওই বছরই রোগশয্যায় তিনি কিছুটা ক্ষোভ, কিছুটা অভিমান নিয়ে এক সাক্ষাৎকারে বলেছিলেন, ‘কাব্য সাহিত্যের ইতিহাসে গীতিকারদের স্থান দেওয়া হয় না। এ বড় ক্ষোভের কথা।
অজয় ভট্টাচার্য, শৈলেন রায়, মোহিনী চৌধুরী প্রমুখ গীতিকারদের কবি প্রতিভা সম্বন্ধে কারও কোনও সন্দেহ থাকার কথা নয়। তবু কবি সম্মেলনে কোন গীতিকারকে ডাকা হয় না। কবিতায় সুর দিলেই গান হয় না। গানের ভাষা সম্পূর্ণ আলাদা। তা না হলে রবীন্দ্রনাথ কবিতা ছাড়াও অত গান লিখতেন না।’ এর পরই গৌরীপ্রসন্ন মোক্ষম কথাটা বলেছেন, ‘তিনি (রবীন্দ্রনাথ) যে নোবেল পুরস্কার পেয়েছেন, তা একটি গানের বইয়ের জন্য।’
৩.
তর্কটা উসকে দিয়ে সেটা এখন তুলে রাখার সময় হলো। ফিরি গৌরীপ্রসন্ন মজুমদারের কৃতিত্বে। তার কীর্তির কথা তো লিখে রেখেছে ইতিহাস। গৌরীপ্রসন্ন মজুমদারের লেখা বহু গান কালজয়ী হয়েছে। কিন্তু, তার কবিপ্রতিভার হদিস চরমভাবে পাই আরতি মুখোপাধ্যায়ের গাওয়া ও নচিকেতা ঘোষের সুর করা ‘এই মোম জোৎস্নায় অঙ্গ ভিজিয়ে এসো না গল্প করি’ গানটিতে। আরতি ও নচিকেতা বাংলা সঙ্গীতের দুই দিগগজ।
গীতিকার-সুরকার-কণ্ঠশিল্পী – একই গানে তিন কিংবদিন্ত মিলিত সৃষ্টি করেছেন এক অনন্য সঙ্গীত, এটা খুব একটা ঘটতে যায় না। কিন্তু, এই অসামান্য ঘটনার পেছনে ঢেকে গেছে একজন কবির দুর্দান্ত এক কবিতা। যে কেউই কবিতার মতো করে পড়লে সেটা বিলক্ষণ বুঝবেন। তারুণ্যে ইংরেজি কবিতা লিখে হাত পাকানো গৌরীপ্রসন্ন মজুমদার বাংলা সঙ্গীতে এমন অনেক কবিতা উপহার দিয়েছেন, যেগুলো সাহিত্যের বিচারে মূল্যায়িত হয়নি।
সঙ্গীত-জগতেও কি সঠিকভাবে মূল্যায়িত হয়েছে তার কীর্তি? এত বড় একজন গীতিকার, মনে হয় না, নতুন প্রজন্মের সঙ্গীত জগতের সঙ্গে সংশ্লিষ্টরা খুব গভীর অনুধ্যান দিয়ে তাকে পাঠ করেছেন। তার লেখা বিখ্যাত গান নিয়ে বিস্তারিত লিখতে গেলে এ লেখা শেষ হবে না।
সঙ্গীত সাধনার একদম শুরুর দিকেই পেয়েছিলেন শচীন দেববর্মণের সান্নিধ্য। এ সান্নিধ্য এতটাই গভীরে রূপ নিয়েছিল যে, উভয়ের কেমেস্ট্রিতে সৃষ্টি হয়েছিল ‘মেঘ কালো আঁধার কালো’, ‘বাঁশি শুনে আর কাজ নাই’ ইত্যাদি সঙ্গীত।
শুধু শচীন দেব বর্মণ নয়, কিশোর কুমার, লতা মঙ্গেশকর, আশা ভোঁসলে, হেমন্ত মুখোপাধ্যায়, মান্না দে, রাহুল দেববর্মণ, সন্ধ্যা মুখোপাধ্যায়, আরতি মুখোপাধ্যায়… কে গাননি তার লেখা গান!
লিখেছেন ‘প্রেম একবার এসেছিল নীরবে’, ‘কী আশায় বাঁধি খেলা ঘর বেদনার বালুচরে’, ‘এই সুন্দর স্বর্ণালী সন্ধ্যায় এ কী বন্ধনে জড়ালে গো বন্ধু’ ‘ও নদী রে/ একটি কথা শুধাই শুধু তোমারে’, ‘নীল আকাশের নীচে’, ‘তারে বলে দিও’, ‘আজ দু’জনার দু’টি পথ’, ‘মুছে যাওয়া দিনগুলি’, ‘এই রাত তোমার আমার’, ‘পথের ক্লান্তি ভুলে’, ‘এই পথ যদি না শেষ হয়’, ‘এই মেঘলা দিনে একলা ঘরে থাকে না তো মন’, ‘কেন দূরে থাকো শুধু আড়াল রাখো’, ‘আমার গানের স্বরলিপি’, ‘আমার স্বপ্নে দেখা রাজকন্যা থাকে’ ইত্যাদি বহু বিখ্যাত গান।
ইচ্ছে করেই কণ্ঠশিল্পী ও সুরকারের নাম লিখে লেখার মেদ বাড়ালাম না। তবে, একজন সুরকারের নাম উল্লেখ না করলেই নয়। তিনি হলেন নচিকেতা ঘোষ। গৌরীপ্রসন্ন মজুমদারের নাম উঠলেই নচিকেতা ঘোষের নামও উঠবে সঙ্গীত পরিচালক ও সুরকার হিসেবে। নচিকেতা ঘোষের প্রায় সত্তর ভাগ গানের গীতিকার গৌরীপ্রসন্ন মজুমদার। ঘটনাচক্রে, তার ঘনিষ্ঠতম বন্ধুটির মতো তিনিও আরেক পর্দার আড়ালের মানুষ। অথচ, তার অবদানও মহীরুহসম। নিশ্চয়ই কোন না কোন সময়ে কারও না কারও গবেষক-মনন বাংলা সঙ্গীতে এই দুই সঙ্গীত সাধকের যৌথ অবদানের কথা তুলে ধরবেন।
শেষ করি তার বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধে অবদানের কথা উল্লেখ করে। মুক্তিযুদ্ধ শুরু হওয়ার অনেক আগেই পাবনার ভিটে ছেড়ে তিনি পাড়ি দিয়েছেন কলকাতায়। সময়টা ১৯৬৫ সাল। ফলে, এখানকার সব খবরাখবর সবার মতো তিনিও পাচ্ছিলেন রেডিওতেই। ১৯৭১ সালের ৭ মার্চ বঙ্গবন্ধুর সেই বিখ্যাত ভাষণ তিনি শুনেছিলেন আকাশবাণীর অবসরপ্রাপ্ত কর্মকর্তা শ্রীতরফদারের রেকর্ড প্লেয়ারে।
অনলবর্ষী সেই বক্তৃতা শুনে গৌরীপ্রসন্ন মজুমদার ওই আড্ডাতেই সিগারেটের প্যাকেটের সাদা কাগজে লিখলেন কালজয়ী সেই গান ‘শোনো, একটি মুজিবরের থেকে/ লক্ষ মুজিবরের কণ্ঠস্বরের ধ্বনি-প্রতিধ্বনি/ আকাশে-বাতাসে ওঠে রণি/বাংলাদেশ, আমার বাংলাদেশ’। গানটি সুর করলেন ও গাইলেন অংশুমান রায়। বাংলাদেশের অস্থায়ী সরকারের শপথ অনুষ্ঠানে বাজানো হয় এই গান। এই গানটি পরে ‘মিলিয়ন মুজিবর সিঙ্গিং’ নামে অনুদূতিও হয় ইংরেজিতে। বাংলাদেশ স্বাধীন হওয়ার পর বঙ্গবন্ধুর আমন্ত্রণেই বাংলাদেশে এসে বাংলাদেশ বেতারের জন্য তিনি লিখেছিলেন, ‘মাগো ভাবনা কেন/ আমরা তোমার শান্তিপ্রিয় শান্ত ছেলে’ গানটি। গানটি হেমন্ত মুখোপাধ্যায়ের কণ্ঠে সৃষ্টি করেছিল তুমুল আলোড়ন।
৪.
বিশ শতকের মধ্যভাগে বাংলা সঙ্গীতের মহাপ্রাচুর্যে ও স্বর্ণসময়ে নিজের আগমন ঘোষণা করা গৌরীপ্রসন্ন মজুমদার আধুনিক বাংলা সঙ্গীতে গীতিকার হিসেবে এতটাই মৌলিকত্ব বহন করেন যে, তার অবস্থান ঠিক সেই বন্ধনীতেই হওয়া দরকার, যেখানে রবীন্দ্র-নজরুলের পরেই বিরাজ করেন দিজেন্দ্রলাল রায়-রজনীকান্ত কিংবা অতুলপ্রসাদ সেন। উল্লেখিত প্রত্যেকেই কবি হিসেবেও আমাদের পাঠযোগ্য হয়েছেন, তাহলে গৌরীপ্রসন্নের কমতিটা কোথায়?
শচীন দেব তাকে বলতেন, ‘কলকাতার মজরুহ্ সুলতানপুরী’, এই তকমার প্রতি সুবিচার তিনি করতে পেরেছিলেন কি না, সেটার বিচার করবে ইতিহাস, কিন্তু, গৌরীপ্রসন্ন মজুমদার সন্দেহাতীতভাবে বাংলা সঙ্গীতের এক ধ্রুবতারা। তিনি ‘আনসাং হিরো’ হতে পারেন, কিন্তু তাকে আমাদের স্মরণ করা জরুরি। তার প্রতি শ্রদ্ধা, তার প্রতি কুর্ণিশ।
তথ্যসূত্র:
সারেগামা বেঙ্গলী উইকেন্ড ক্লাসিক্স রেডিও শো – গৌরীপ্রসন্ন মজুমদার স্পেশাল।
‘পরোটা-মাংস খেয়ে লিখলেন ‘আমার গানের স্বরলিপি’, দৈনিক আনন্দবাজার পত্রিকা, ৪ জানুয়ারি ২০২০।
শিতাংশু গুহ, ‘গৌরী প্রসন্ন মজুমদার: মুক্তিযুদ্ধে তার অবদান অনস্বীকার্য’, দৈনিক ভোরের কাগজ, ১২ ডিসেম্বর ২০১৮।
জন্ম ও মৃত্যু:
গৌরীপ্রসন্ন মজুমদার ১৯২৪ সালে ৫ ডিসেম্বর বর্তমান বাংলাদেশের পাবনা জেলার ফরিদপুর উপজেলার গোপালনগর গ্রামে জন্মগ্রহণ করেন। বাচ্চু’ ছিল তার ডাক নাম। তার বাবা গিরিজাপ্রসন্ন মজুমদার ছিলেন বিখ্যাত উদ্ভিদবিদ। গৌরীপ্রসন্ন ১৯২৪ খ্রিষ্টাব্দের ৫ই ডিসেম্বর জন্মগ্রহণ এবং ১৯৮৬ সালের ২০ আগস্ট কলকাতায় মৃত্যু বরণ করেন।
আরও দেখুন: